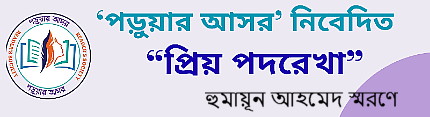এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিন
এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিনআবু এন. এম. ওয়াহিদ  ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ -১০ এপ্রিল ১৯৩১ কোনো এক দ্বীপদেশের এক অগ্রগামী অগ্রদূত, দেশ ছেড়ে অনেক দূরে প্রবাসে থাকেন, স্বপ্ননগরী ওরফালেসে। অগ্রদূত একজন মহাপুরুষ। তিনি তাঁর প্রভুর প্রিয়পাত্র এবং সঠিক সত্যপথের অনুসারী। তাঁর নাম আল-মুস্তাফা। আল-মুস্তাফা, ওরফালেসে এসে যখন সত্য প্রচার শুরু করেন, তখন যে ব্যক্তি প্রথম তাঁর কথায় আস্থা রেখে তাঁর ভক্ত অনুসারী হন, তিনি একজন নারী। তাঁর নাম আল-মিত্রা। প্রবাস-জীবনে আল-মুস্তাফা, ওরফালেস মহানগরে সাধারণ মানুষদের সাথে অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। তাদের সুখ-দুঃখ নিজের সাথে ভাগাভাগি করে নেন, সময় সময় তাদের বুদ্ধি-পরামর্শ দেন এবং এভাবে অল্প দিনেই তিনি অসংখ্য গণ-মানুষের হৃদয়ে নিজের স্থান চিরস্থায়ী করে নেন। ওরফালেসে বারো বছর বসবাসের পর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আল-মুস্তাফা যেদিন জাহাজে উঠতে যাবেন, সেদিন তাঁর অনুসারী লক্ষ লক্ষ নগরবাসী তাঁকে বিদায় জানাতে দলে দলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত সাগরপারের ধর্মশালার সামনে জনমানুষের জমায়েত রূপ নেয় এক জনসমুদ্রে। বিদায় বেলায় প্রাণপুরুষকে কাছে পেয়ে নগরবাসী একে একে উত্থাপন করে রহস্যময় জীবন-জিজ্ঞাসার নানা প্রসঙ্গ। আর তিনি উদাহরণ ও গল্পের ছলে তাদেরকে বোঝান অর্থপূর্ণ মানবজীবনের বিভিন্ন দিক। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনায় ওঠে আসে ভালোবাসা ও ঘরসংসারের কথা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম, ছেলেমেয়ে, খাওয়াপরার কথা। সমাজ, ন্যায়-অন্যায়, আইন-কানুন, বিচার-সালিশের কথা। সৌন্দর্য, আনন্দ, জীবন-মৃত্যু, ধর্ম ও প্রভুর কথা। আলোচনা শেষে আল-মুস্তাফা ধীরে ধীরে গিয়ে জাহাজে ওঠেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ জনতার মুখোমুখি হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে উঁচু-স্বরে তিনি তাঁর বিদায় বেলার শেষ বক্তব্য রাখতে থাকেন। জাহাজ আস্তে আস্তে সমুদ্রতীর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আল-মুস্তাফার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হয়ে। ততক্ষণে অরফালেসবাসী যার যার বাড়িঘরে ফিরে গেছেন। আল-মিত্রা একা দাঁড়িয়ে আছেন সাগরপারে। তিনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন সীমাহীন জলরাশির দিকে। তাঁরই অশ্রু-বাষ্পে আবছা হয়ে যাওয়া জাহাজ ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার বাইরে গিয়ে দিগন্তরেখার সাথে মিলিয়ে যায়! আল-মিত্রা ভাবতে থাকেন আল-মুস্তাফার কথা - ‘কে তিনি? কেন এলেন? কেন ফিরে গেলেন? আর কোথায়ই-বা তাঁর দেশ?’ এ কাহিনী বর্ণিত আছে, বিখ্যাত ‘দি প্রফেট’ গ্রন্থে। এতে আছে ২৬টি কাব্যিক প্রবন্ধ। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯২৩ সালে, কিন্তু এটা প্রথমবারের মত আমেরিকার কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অনেক পরে, ১৯৬০-এর দশকে। তারপর দুনিয়া-ব্যাপী বইটির চাহিদা এতই বেড়ে যায় যে, আজ অবধি পৃথিবীর ৪০টি ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। বইটি কখনোই ‘আউট অফ প্রিন্ট’ হয়নি। এই বইয়ের লেখক একজন প্রতিভাবান ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি জন্ম নিয়েছিলেন মানব সভ্যতাকে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সবকিছু উজাড় করে দিয়ে যেতে এবং দিয়েও গেছেন। প্রতিদানে তিনি কিছুই চাননি, পাননি, নেনওনি। উপরন্তু তাঁর অফুরন্ত সেই ভাণ্ডার শেষ হওয়ার আগেই সবাইকে ফাঁকি দিয়ে তিনি চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে! তিনি আর কেউ নন। চিন্তাবিদ, দার্শনিক, চিত্রশিল্পী, ও কবি কাহ্লিল জিবরান। অনেক ভেবেচিন্তেও আমি জিবরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত বই ‘দি প্রফেট’ এর একটি রহস্যের কোনো হদিস পাইনি। রহস্যটি হলো – জিবরান জন্মেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন আরবিভাষী দেশ লেবাননে রক্ষণশীল খ্রিষ্টান পরিবেশে। ছোটবেলায় খ্রিস্টধর্মে শিক্ষা নিয়েছেন পাদ্রীর কাছে। ‘মুস্তাফা’ ইসলামের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আরেক নাম। এটা কোনো অবস্থাতেই তাঁর না জানার কথা নয়। তারপরও, একজন খ্রিষ্টান হয়ে, তিনি তাঁর ‘দি প্রফেট’ গ্রন্থের মূল চরিত্রের নাম কেন ‘আল-মুস্তাফা’ দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখনও খুঁজছি। আমার সাম্প্রতিক বৈরুত সফরে এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার এক লেবানিজ অধ্যাপক বন্ধুর সাথে। তিনি বললেন, ‘বিবদমান খ্রিষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ার তাগিদে জিবরান সচেতনভাবেই এ কাজটি করে গেছেন।’ আমার বন্ধু মাহবুব চৌধুরীর মতে, এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। সে মনে করে, এ রহস্যের জট খুলতে গেলে আগে জানতে হবে জিবরানের ‘প্রফেট’ আসলে কে? জিবরানের ‘প্রফেট’ আর কেউ নন, তিনি নিজেই। তাঁর কাব্য-প্রবন্ধের বই ‘দি প্রফেট’-এর মূল চরিত্র আল-মুস্তাফার মুখ দিয়ে জিবরান প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কথাগুলোই বলে গেছেন। জিবরান-গবেষকদের মধ্যে এ রকমের একটা ধারণা চালু আছে যে, জিবরান নিজেকে একজন ‘প্রফেট’ মনে করতেন, যদিও এ কথা তিনি কখনো মুখ ফুটে বলেননি। তার কারণ কী সেটা জানা যায় না, তবে তাঁর চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা, তাঁর জীবনবোধ ও জীবন ধারণের নমুনা দেখলে তেমনটাই মনে হয়। রক্ষণশীল খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিয়ে এবং খ্রিষ্টান পরিবেশে বড় হয়ে, নিজেকে ‘প্রফেট’ মনে করে জিবরান যেসব কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে খ্রিস্টধর্মের চৌহদ্দি পেরিয়ে গেছে। কারণ তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র আল-মুস্তাফা যিশু খ্রিষ্টের মত শুধু ‘প্রেম-ভালোবাসা’র কথা বলেননি, ‘এক গালে চড় খেলে আরেক গাল পেতে দিতে’ও বলেননি। আল-মুস্তাফা কঠিন-কঠোর বাস্তব জীবনের খুব কাছাকাছি ছিলেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের সকল শাখা-প্রশাখায় তাঁর বিচরণ ছিল সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের সকল সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা সমান গুরুত্ব দিয়ে অনুভব করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, মানব জীবনকে সার্বিকভাবে জানা, বোঝা, উপলব্ধি করা এবং সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে প্রচার করার এ অফুরন্ত শক্তি জিবরান কোথায় পেলেন? এ প্রসঙ্গে সহজেই এ কথা বলা যায় যে, তিনি এই ধারণা খ্রিষ্টীয় ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্য থেকে পাননি। এটা হয়তো বা প্রকৃতি-প্রদত্তভাবে একান্তই তাঁর নিজস্ব শক্তি, যা তিনি নিজেই ধারণ ও লালন করেছেন। অথবা হতে পারে, তিনি মানব জীবনের ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে জীবনকে সার্বিকভাবে দেখার দীক্ষা পেয়েছেন কোরআন পড়ে। আর তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-কীর্তি - ‘দি প্রফেট’-এর মূল চরিত্রের নাম ‘আল-মুস্তাফা’ রেখে এ সত্যতারই একটা সরল স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছেন। শুধু ইসলামই নয়, কিতাব-প্রাপ্ত অন্য দুই ধর্ম - যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিও জিবরানের গভীর অনুরাগ ছিল। এই তিনটি ধর্ম নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা ও গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন। তাঁর লেখালেখি ও দর্শনে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ইসলামের তাসাউফ শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহ্লিল জিবরান ১৮৮৩ সালের ৬ই জানুয়ারি বর্তমান লেবাননে অবস্থিত বির্শারি নামক পাহাড়ি পল্লীতে এক মেরোনাইট খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খলিল জিবরান। তিনি নিজের নামেই ছেলের নাম রেখেছিলেন, খলিল জিবরান, সে নাম কী করে ‘কাহ্লিল জিবরান’ হলো সে কথায় আবার ফিরে আসব পরে। জিবরানের মায়ের নাম ছিল কামিলা রাহমাহ। কামিলার বাবা ছিলেন একজন পাদ্রী। জিবরান তাঁর মা-বাবার তৃতীয় সন্তান। জিবরানের বাবা ছিলেন তাঁর মায়ের তৃতীয় স্বামী। মূলত অভাব-অনটনের কারণে ছোটবেলায় জিবরানের স্কুলে যাওয়া হয়নি। একা একা তিনি পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গভীরভাবে অবলোকন ও উপভোগ করতেন! পরবর্তীকালে তাঁর লেখায় এবং ছবি আঁকায়, পাহাড়, পর্বত ও প্রকৃতির প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। জিবরানের মা কামিলা ছিলেন একটি রক্ষণশীল খ্রিষ্টান পরিবারের মেয়ে। তাই তাঁদের বাড়িতে ধর্ম-শিক্ষাদানের জন্য ঘন ঘন একজন পাদ্রীর আনাগোনা ছিল। ঐ পাদ্রীর কাছে ভাসা ভাসা ভাবে, জিবরান বাইবেলের সাথে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও আরবি ভাষা শেখেন। দুষ্টু জিবরান দশ বছর বয়সে খাড়া পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে নিজ ঘাড়ের বাঁ দিকে মারাত্মক জখম করে ফেলেন। সময়মত সঠিক চিকিৎসার অভাবে আমৃত্যু তাঁর ঘাড়ের বামদিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। জিবরানের বাবা প্রথম দিকে এক ঔষধ কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর জীবন ছিল খুবই ছন্নছাড়া ও অগোছালো। তিনি জুয়া খেলায় আসক্ত ছিলেন, যে কারণে সব সময় থাকতেন ঋণগ্রস্ত। পরে তিনি এক অটোমান আঞ্চলিক সরকারি কর্মকর্তার অধীনে কাজ নিয়েছিলেন। লেবানন তখন ছিল সিরিয়ার অঙ্গীভূত; আর সিরিয়া ছিল অটোমান সম্রাজ্যের অংশ। জিবরানের জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স ছিল ৩০। জিবরানের বয়স যখন মাত্র আট, তখন কর ফাঁকির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর বাবাকে জেলে যেতে হয়েছিল। ওই মামলায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ফলে কামিলা জিবরান, জিবরানের সৎভাই পিটার এবং দুই বোন মারিয়ানা ও সুলতানাকে নিয়ে গৃহহীন হয়ে পড়েন। কামিলা ঘুরেফিরে আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তখন জিবরানের এক মামা থাকতেন আমেরিকায়। ভাইয়ের পথ অনুসরণ করে ভাগ্য বদলের আশায় অনেক সাহস করে, কামিলা ১৮৯৫ সালের ২৫শে জুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে জাহাজযোগে বৈরুত থেকে আমেরিকার নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তার কিছুদিন আগে জিবরানের বাবা জেল থেকে ছাড়া পান বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতার কারণে তিনি পরিবারের সাথে আমেরিকা না এসে লেবাননেই থেকে যান। জিবরানের মা আমেরিকাতে এসে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ঐতিহাসিক বোস্টন শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বসতি স্থাপন করেন। ওই সময় দক্ষিণ-বোস্টনে জিবরানের মামাসহ আরবিভাষী অনেক সিরিয়ান ও লেবানিজ লোক থাকতেন। অন্যান্য সিরিয়ান মহিলাদের সাথে জিবরানের মা এক পোশাক তৈরির কারখানায় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেইস ও লিনেন দ্রব্যাদি বিক্রি করতে থাকেন। আমেরিকা আসার দু’মাস পর ১৮৯৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ‘খলিল জিবরান’ গিয়ে স্কুলে ভর্তি হলেন। সে সময় ভুলবশত: স্কুলের রেজিস্ট্রি বইয়ে তাঁর নাম Khalil Jibran - এর বদলে Kahlil Jibran লেখা হলো। এভাবে তাঁর বাবার দেওয়া আসল নাম বিকৃত হয়ে গেলো এবং জিবরানও পরে আর সে নাম শুধরোবার কোনো তাগিদ অনুভব করেননি। যেহেতু তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার কোনো রেকর্ড ছিল না, তাই অন্যান্য সব অভিবাসী ছেলেমেয়েদের সাথে ইংরেজি শেখার জন্য তাঁকে একটি বিশেষ ক্লাসে ভর্তি করা হলো। ছোটবেলা থেকেই জিবরান নিখুঁত ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর এই বিরল প্রতিভা অচিরেই শিক্ষকদের নজর কাড়ে। স্কুলের শিক্ষকদের সহায়তায় জিবরানের যোগাযোগ হয় তখনকার সময়ে বোস্টনের একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ফ্রেড হল্যান্ড ডে-র সাথে। ফ্রেড ডে জিবরানকে এতই পছন্দ করে ফেলেন যে, তিনি সাথে সাথে জিবরানের ম্যান্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফ্রেড ডে, জিবরানকে বলতেন ‘ন্যাচারাল জিনিয়াস’। ফ্রেড ডে-র উৎসাহে এবং আনুকূল্যে জিবরান বইয়ের কাভার ডিজাইন, স্টোরি ইলাস্ট্রেশন এবং পোট্রেট আঁকার কাজ পেতে থাকলেন। এভাবে ছবি-আঁকা ও চিত্রশিল্পের মহাজগতের সিংহদ্বার জিবরানের জন্য অতি সহজেই খুলে গেল!         পরের অংশ পরের অংশ  |