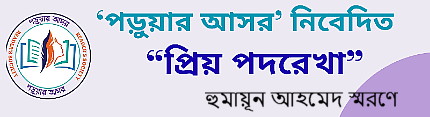এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিন
এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিনঅধ্যাপক শামস্ রহমান  ফিরছিলাম মেলবোর্ন। লিস্বন থেকে। আটলান্টিক পাড় ঘেঁসে এ শহরটি অবস্থিত। আমাদের কাছে লিস্বন নামে পরিচিত হলেও, স্থানীয়দের কাছে তা লিশ্বোয়া। লিশ্বোয়া থেকে লস্বন! কি অদ্ভুত রূপান্তর! ওরা কি কারও উপনিবেশ ছিল কখনো? আমরা ছিলাম। তাই আমাদের ঢাকা হয় ডাক্কা, আর মুম্বাই হয় বোম্বে। দুটো নামের পরিবর্তন হয়েছে বটে, অন্ততঃ মিল আছে ছন্দে। কিন্তু চেন্নাইয়ের রূপান্তর? চেনাই যে মাদ্রাজ, তাতো চেনাই মুস্কিল। অনেকটা গৃহস্থালি কাজে সাহায্যকারীদের যেমন খুশী তেমন নাম রাখার মতন। ফিরছিলাম মেলবোর্ন। লিস্বন থেকে। আটলান্টিক পাড় ঘেঁসে এ শহরটি অবস্থিত। আমাদের কাছে লিস্বন নামে পরিচিত হলেও, স্থানীয়দের কাছে তা লিশ্বোয়া। লিশ্বোয়া থেকে লস্বন! কি অদ্ভুত রূপান্তর! ওরা কি কারও উপনিবেশ ছিল কখনো? আমরা ছিলাম। তাই আমাদের ঢাকা হয় ডাক্কা, আর মুম্বাই হয় বোম্বে। দুটো নামের পরিবর্তন হয়েছে বটে, অন্ততঃ মিল আছে ছন্দে। কিন্তু চেন্নাইয়ের রূপান্তর? চেনাই যে মাদ্রাজ, তাতো চেনাই মুস্কিল। অনেকটা গৃহস্থালি কাজে সাহায্যকারীদের যেমন খুশী তেমন নাম রাখার মতন। উপনিবেশ নয়, লিশ্বোয়ার অধিবাসীরা নিজেরাই ছিল উপনিবেশিক শক্তি। ভাস্কো-দা-গামা, সাগর-অভিযাত্রী, লুটেরা, বণিক এসবের সবই তারা। এক সময় আমাদের ঘরবাড়ী উঠোন ছিল অন্য আর এক উপনিবেশিক শক্তি দখলে। উপনিবেশিক শক্তি আর অভ্যন্তরীণ মারাঠা বর্গীদের উদ্দেশ্যে তেমন কোন তফাৎ ছিল কি? লুট, খাজনা, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, তখন এসবই ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে। - এই পঙ্কতিগুলি মাঝেই কিছুটা হলেও মেলে বর্গীদের ত্রাসের স্বাক্ষর। উপনিবেশের ধন-সম্পদে গড়া সেই জৌলুস এখন আর নেই লিশ্বোয়ার মসনদে। শহরের অট্টালিকায় তার ছাপ স্পষ্ট। সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর চেপে, ধেয়ে আসার সাহসও আর নেই। ইষ্ট তিমুরকে ফিরিয়ে দেয়া স্বাধীনতাকে ১৯৭৫এ ইন্দোনেশিয়ার আগ্রাসন থেকে রক্ষায় ব্যর্থতাই এর প্রমাণ। অতীতের উড়ে এসে জুড়ে বসার মত জলদস্যু-পনা মনোবৃত্তিরও অভাব এখন। তাইতো ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশী স্প্যানিশ, বিলেতি কিংবা ইতালিয়ানরা ব্যবিলনের ব্যরেলের উপর ঝাণ্ডা উড়ালেও, পর্তুগীজদের জাহাজ নোঙ্গর করেনি শাত-আল-আরবের জলে। এভাবেই হয়তো মেনে নিতে হয় জাতি-জীবন চক্রের বাস্তবতাকে। আজকের মহাশক্তি-দ্বয়ের সাউথ চায়না সির মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ঘটনাও প্রমাণ করে এ চক্রের বাস্তবতা। আজ এ চক্রের শিখরে যাদের অবস্থান, তাদের কি বিশ্বাস আছে এ চিরন্তন সত্যে? থাকলে হয়তো পৃথিবী আরও একটু সুন্দর ও সুখকর হতে পারতো। লিশ্বোয়া থেকে প্লেন এসে নামলো হিথরো। কথায় বলে সস্তার তের অবস্থা। কম নামীদামী এয়ারলাইন্সের টিকেট, তাই তার সীমাবদ্ধতাও অনেক। বিধায়, মেনে নিতে হয়েছে ছঘণ্টার বাধ্যতামূলক যাত্রা বিরতি। এক সময় হিথরো থেকে আবার উড়লো প্লেন। আমার আইলের আসন। এ বয়সে এসে পছন্দের এটাই অগ্রাধিকার। যৌবনে উইন্ডো সিটে বসে আকাশের রঙ দেখার এক দূর্বার আকর্ষণ ছিল। ক্ষণিকের জন্য হলেও ক্ষণিকটা কাছে থেকে আকাশের রঙ আর ক্ষণিকটা উঁচু থেকে ছবির মত সাজানো গোছানো পৃথিবী দেখে ভরে উঠতো মন। কল্পনা আর বাস্তবতার সংঘাতে উইন্ডো সিট এখন বড্ড সাফোকেটিং লাগে। আমার পাশে বসে মার্গারেট (নামটা পরে জেনেছি)। সমার্সেট মমের রচিত Luncheon গল্পের সেই নারী চরিত্রের মতন মার্গারেটের গড়ন। বসে, আসনের পুরো জায়গা জুড়ে। ইকোনোমিক ক্লাসের স্বল্প পরিসরের আসনটি উপচে পড়ে অতি আহারে অর্জিত ওর বাহারের দৈহিক সম্পদ। ভাবি - ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কৃষির ওপর থেকে ভর্তুকির ভার কি কমানো যায় না? অতি আহারের স্থলে, উদ্বৃত্ত, অনাহারীদের প্রাপ্য নয় কি? সবাইতো মানুষ! একই তো পৃথিবী! এ আমার অর্থহীন ইউটোপিয়ান ভাবনা। বাস্তবে খাদ্য একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। তার প্রমাণ তো ৭৪এর দুর্ভিক্ষ। সুজান জর্জের How the other half diesএ খাদ্যাভাবে মৃত মানুষের পরিসংখ্যান কখনও কখনও কঙ্কাল হয়ে ভেসে উঠে আমার ভাবনার জানালায়। মার্গারেটের সাথে হায়, হ্যালো হলো। ব্যস, এ পর্যন্তই। আমাদের সারির উইন্ডো আসনটি দখল করে মধ্য বয়সী এক আইরিশ ভদ্রলোক। প্রাথমিক পরিচয়ের পরই শুরু হল ওদের মাঝে কথোপকথন। প্রথমে আবহাওয়া, কতদূর যাওয়া এবং এটা সেটা। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিককালের বোমা হামলার ঘটনা। আমার সমস্ত মনোযোগ তখন প্লেনের মাইক্রো পর্দায় ঐশ্বরিয়া রায়ের ঐশ্বর্যে ভরা সদ্য মুক্তি পাওয়া একটি সিনেমায়। নাচে গানে ভরপুরের মাঝেও কানে আসে ওদের কথোপকথন। মার্গারেট বলে কোথায় ঘটেছে এ সব ঘটনা। কিভাবে ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ। অনেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা। উল্লেখ করে আহত-নিহতের পরিসংখ্যান। ফাঁকে ফাঁকে নিজের মতামত দিতেও ভুলেনি। তবে আলোচনায় একবারও আসেনি এসব ঘটনার মূল কারণ। কারণ খোঁজা কি এতই সহজ? কারণ, কারণের পিছনে থাকে কারণ। তারও পিছনে থাকে অন্য কারণ। তাই কজ-ইফেক্ট-কজএর প্রক্রিয়ায় মানব ইতিহাসের কোথায় টানবে লাইন? কেইবা টানবে এই লাইন? জাতি-জীবন চক্রের শিখরে যখন যারা, তারা হয়তো শুধুই বাহ্যিক ফলাফলের বিশ্লেষণে বিশ্বাসী, মূল কারণে নয়। তাই ফলাফলের প্রতিক্রিয়ার মাঝে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা বজায় রাখাই তাদের কাম্য। ওদের আলোচনায় আমাকে টানা তো দূরে থাক, মার্গারেট আমার দিকে একবারও ফিরে তাকায়নি। ও কি আমাকে ভয় পেয়েছে? অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, আজ যাদের সন্ত্রাসী বলছি, তাদের সাথে আমার চেহারার যথেষ্ট মিল। কিন্তু উইন্ডো আসনে আসীন আইরিশ ভদ্রলোক? যার সাথে এতটা সময় কথোপকথনে মশগুল, সে উত্তরের না প্রজাতন্ত্রের তা কি মার্গারেট জানে? আমার ডান পাশে আইল। প্লেন ওড়ার পর এ পথ ধরেই প্রথমে আসে পরীর দল, সঙ্গে নিয়ে জীন। বলে এগুলো মানুষের জন্য? সেবার যেন অন্ত নেই! জীন, পরী আর মানুষের এই সুমধুর সখ্যতা শূন্যেই বুঝি সম্ভব! আইলের ঠিক ওপাশে এক বয়স্ক মহিলা বসা। বয়সে পঁচাত্তর পেরিয়ে গেছে তাও অর্ধযুগেরও বেশী হবে বলে বিশ্বাস। বসে আছে চুপচাপ। মনে হয় কিছুটা কাহিল। মাথাটা বারবার নুইয়ে পড়ছে। বিমানবালা এলো পানি নিয়ে। ভদ্রমহিলা ট্যাবলেট খেল। কিছু জিজ্ঞেস করব কি করব না, ভাবছিলাম। এক সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে বলে বসলাম, আর ইউ অল রাইট? কোন উত্তর নেই। শুধু দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। তার পড়নে সালোয়ার-কামিজ। গড়নে লম্বা। দেখতে ফর্সা আর টানা মুখমণ্ডল। দীর্ঘ নাসিকা ও গ্রীবা। ছেলে বেলায় মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে দেখা নেকাবে ঢাকা রমণীর মত যেন। উত্তর না পেয়ে বললাম, আপকা বেরাম হ্যাঁয়? আমার উর্দু-হিন্দির দৌড় যে কতদূর, তা তো আমার জানা। এবার উত্তরে শুধু বললেন, বেরাম। বাংলা উচ্চারণের হের-ফেরে উচ্চারিত বাক্যটি ব্যাকরণের বিধিনিষেধ অমান্য করলেও, প্রয়োগের বাস্তবতায় পেরিয়ে গেল হিমালয়। আমার সাহস তখন বেড়ে দ্বিগুণ। বললাম, আপ্কা কুছ লাগেগা তো, হাম বলায়ে। ঠিক হায়? ভদ্রমহিলার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখন। চোখে দুটো চঞ্চল দেখায়। আর ঠোটের কোণায় এক টুকরো মৃদু হাসি। মুখে কিছু বলল না। শুধু রাযিয়ার মত দীর্ঘ বাহুটা সম্প্রসারিত করে চেপে ধরেন আমার বাহু। মনে মনে বললাম এত অল্পতে কাউকে এতটাই খুশী করা যায়? তখন হঠাৎ মনে পরে সোহেল কায়সারের কথা। এ আই টিতে মাস্টার্স করার সময় পরিচয়। পাঞ্জাবী যুবক। আমার বাংলাদেশী বাঙ্গালি হিসেবে প্রথম পরিচয়েই জিজ্ঞেস করে বসে কিয়া হাল হায়? ও ধরেই নেয়, আমি উর্দু বাৎচিত জানি। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার প্রশ্ন আপ্ কাহান রাহ্তি হায়েন? এমন এক ভাব যে আমাকে উর্দু জানতেই হবে! এ যেন চাপিয়ে দেওয়ার এক মনোবৃত্তি। সেদিন সোহেলের হাবভাবে উপনিবেশিক মানসিকতার প্রকাশ ছিল স্পষ্ট। উত্তরে আমি বলি হোয়াট? তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যন্ড উর্দু? আমি বলি নো। এ ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর অন্তর সোহেলের সাথে আবার দেখা। ব্যংককে এক কনফারেন্সে। আমি যে উর্দু বুঝি না এতদিন পরও সে মনে রেখেছে। তাই এবারের কথোপকথন ইংরেজিতেই চলে। উর্দু যে আমি একদম বুঝি না, তা তো নয়। তবে সেদিন অস্বীকার করে এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর পরেও তথ্যটা সোহেলের মনে রাখার কারণে কোথায় যেন একটু সুখ সুখ গন্ধ পাই। আর আজ নিজের অপারগতাকে অতিক্রম করে সেই উর্দু-বাংলার মিশ্রণে দুটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যের সৃষ্টির মাঝে এক অসুস্থ বৃদ্ধার হ্রদয়ে সাহস জোগাতে পেরে, আমার সুখ সুখ অনুভূতি সেদিনের তুলনায় শত গুণ বেশী। আসলে, জোর-জুলুম বা অযৌক্তিকভাবে চাপিয়ে দিয়ে আর যাই হোক, মন জয় করা যায় না। এটা ঘটে সহজাত নিয়মে। উর্দু ভাষী আবু সায়ীদ আইয়ুব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভাষা বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনিই প্রথম, যিনি রবীন্দ্র সমালোচনায় একটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্য তত্ত্ব ও সুচিন্তিত মেথডোলোজি প্রবর্তন করেন। এত বড় মাপের একজন বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি চাপে ঘটেনি। আবু সায়ীদ আইয়ুব তার লেখা গ্রন্থ আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথএ বলেছেন ইংরেজিতে গীতাঞ্জলী পড়ে মুগ্ধ হয়ে বাংলা ভাষায় গীতাঞ্জলী পড়ার দুর্দম আগ্রহই আমাকে বাংলা শিখতে বাধ্য করে। ভাষায় ঘটে আদান-প্রদান, গড়ে ওঠে সম্পর্ক। সম্পর্ককে ঘিরে শুরু হয় বসবাস। আর বসবাসের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার ছোঁয়ায় রূপ নেয় পোশাক-আশাকের ধাঁচ, আহার-নিদ্রার অভ্যাস। আর এসব মিলেই বিকশিত হয় সংস্কৃতি। তাই ভাষার ওপর আঘাত সংস্কৃতির ওপর আঘাতের সমতুল্য। ৪৮এ যে নীতিগত ভুলের সূত্রপাত হয়, তা সংশোধন হতে ঠেকে ৫২এর দোরগোড়া। তার মাঝে ঝরে অনেক রক্ত। মেলবোর্নে পৌঁছে যে যার পথে ছুটে। মার্গারেট, আইরিশ ভদ্রলোক আর সেই অসুস্থ বৃদ্ধা হুইল চেয়ারে দ্রুত গতিতে হারিয়ে যায় জনসমুদ্রে। হঠাৎ পাশে এক শিশুর কান্না - ভাষাহীন সার্বজনীন ভাষা, আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয়। সে আর এক গল্প...। অধ্যাপক শামস্ রহমান, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া |