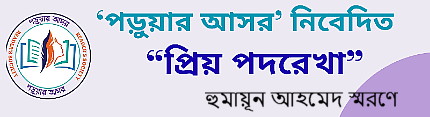ড. রতন কুন্ডু পূর্বরাগ:  মথুরার লবঙ্গ-হ্রদের কিনার ঘেঁষে মধ্য-বসন্তের সূর্য যখন আস্তে আস্তে নিমজ্জিত হচ্ছে, একটি সিঁদুর লাল আভা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। সাদাকালো মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে দিগন্তের কিনারায়, পাখিরা ফিরে আসছে ক্লান্ত ডানায়। ঝিঝি পোকারা গলা ছেড়ে ভৈরবী গাইছে ক্লান্ত দিনকে বিদায় জানাতে। দখিনা হাওয়া গন্ধরাজের সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে মথুরার আকাশে। ধুপছায়া খেলা করে বিরাণ মাঠে। তখন পূব গগনে পূর্ণ বিভাবরী ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়। এমনি লগ্নে ধীরপায়ে হ্রদের কিনারে হেটে আসে এক অনঙ্গ যুবতী। হাতে তার সেমিজ, কাঁচুলি আর প্রসাধনী। পায়ে তার মল, বঙ্কিম কোমরে বিছা, গ্রীবায় স্বর্ণশেকল, কপালে চন্দন তিলক আর চোখের তারায় মধুর ঝিলিক। যুবতী একে একে সব বসন খুলে ফেলেন। প্রকৃতি হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অপরূপ সৌন্দর্যের বন্যায় দক্ষিণ হাওয়ারা থেমে যায়। ঝিঝি পোকারা চুপ হয়ে যায়। পাখির কলকাকলি থেমে যায়। যুবতীর কেশরাজির বিন্যাস মসৃণ গ্রীবা পার হয়ে বাঁক নেয় তাঁর নগ্ন-পৃষ্ঠে। নিটোল পায়ের পায়েল বেজে ওঠে অপূর্ব ঝংকারে। যুবতী পেছনে ফেরে। নটরাজের নাচের মুদ্রা তুলতেই যুবতীর উন্নত বক্ষদেশ দৃশ্যমান হয়। আকাশ জোড়া ক্যানভাসে সেই বিমূর্ত শিল্প মূর্ত হয়। ঠিক সেই সময়েই বনের সরুপথে ক্লান্ত বিকেলে শ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরছিলেন এক তরুণ যুবা। হঠাৎ অপরূপ দৃশ্য দেখে তার হৃদয়ে কাঁপন ধরে। অপলক চেয়ে থাকে লবঙ্গ-হ্রদের চিত্রপটে। তিনি দৃশ্যপট থেকে দৃষ্টি সরাতে পারেননা। হঠাৎ প্রকৃতি খিল খিল করে হেসে ওঠে। সুন্দরী হ্রদের জলে দেহ-বল্লরী নিমজ্জিত করে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। মথুরার লবঙ্গ-হ্রদের কিনার ঘেঁষে মধ্য-বসন্তের সূর্য যখন আস্তে আস্তে নিমজ্জিত হচ্ছে, একটি সিঁদুর লাল আভা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। সাদাকালো মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে দিগন্তের কিনারায়, পাখিরা ফিরে আসছে ক্লান্ত ডানায়। ঝিঝি পোকারা গলা ছেড়ে ভৈরবী গাইছে ক্লান্ত দিনকে বিদায় জানাতে। দখিনা হাওয়া গন্ধরাজের সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে মথুরার আকাশে। ধুপছায়া খেলা করে বিরাণ মাঠে। তখন পূব গগনে পূর্ণ বিভাবরী ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়। এমনি লগ্নে ধীরপায়ে হ্রদের কিনারে হেটে আসে এক অনঙ্গ যুবতী। হাতে তার সেমিজ, কাঁচুলি আর প্রসাধনী। পায়ে তার মল, বঙ্কিম কোমরে বিছা, গ্রীবায় স্বর্ণশেকল, কপালে চন্দন তিলক আর চোখের তারায় মধুর ঝিলিক। যুবতী একে একে সব বসন খুলে ফেলেন। প্রকৃতি হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অপরূপ সৌন্দর্যের বন্যায় দক্ষিণ হাওয়ারা থেমে যায়। ঝিঝি পোকারা চুপ হয়ে যায়। পাখির কলকাকলি থেমে যায়। যুবতীর কেশরাজির বিন্যাস মসৃণ গ্রীবা পার হয়ে বাঁক নেয় তাঁর নগ্ন-পৃষ্ঠে। নিটোল পায়ের পায়েল বেজে ওঠে অপূর্ব ঝংকারে। যুবতী পেছনে ফেরে। নটরাজের নাচের মুদ্রা তুলতেই যুবতীর উন্নত বক্ষদেশ দৃশ্যমান হয়। আকাশ জোড়া ক্যানভাসে সেই বিমূর্ত শিল্প মূর্ত হয়। ঠিক সেই সময়েই বনের সরুপথে ক্লান্ত বিকেলে শ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরছিলেন এক তরুণ যুবা। হঠাৎ অপরূপ দৃশ্য দেখে তার হৃদয়ে কাঁপন ধরে। অপলক চেয়ে থাকে লবঙ্গ-হ্রদের চিত্রপটে। তিনি দৃশ্যপট থেকে দৃষ্টি সরাতে পারেননা। হঠাৎ প্রকৃতি খিল খিল করে হেসে ওঠে। সুন্দরী হ্রদের জলে দেহ-বল্লরী নিমজ্জিত করে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।পূর্ব কথা: অনেক দিনেই ইচ্ছা প্রাগৈতিহাসিক প্রেম কাহিনী লিখব। আম্রপালি ও বিম্বিসার কে নিয়ে লিখলে কেমন হয়? তারপর থেকেই শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে আম্রপালি কে নিয়ে ভাবা শুরু করলাম। এক মধ্যরাতে আমার অনুভবে রবীন্দ্রনাথ এসে হানা দিলেন তাঁর অভিসার নিয়ে। “নগরের নটি চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা, অঙ্গে আঁচল, সুনীল-বরণ রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ, সন্ন্যাসী গায়ে লাগিতে চরণ, থামিল বাসবদত্তা” আমি জানতাম না কবীন্দ্রের এই বাসবদত্তাটা কে! শুরু হল নেট ঘাটাঘাটি। অবাক হয়ে দেখলাম আমার স্বপ্নের আম্রপালি আর কবীন্দ্রের বাসবদত্তা আসলে একই নারী, একই সত্ত্বা, একই কাহিনী। কাগজ কলম তুলে নিলাম। পূর্ণ কাহন: অনেক অনেক দিন আগের কথা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি মথুরা নগরীতে একটি মেয়ে শিশুর চলনে বলনে ভারতনাট্যমের মুদ্রা প্রকাশ পায়! যখন সে হাটে তার পায়ের নূপুর নিক্বণ তোলে বাতাসে। তার এলোমেলো পদভার পৌরাণিক মুদ্রায় হেসে ওঠে।তার হৃদয়-কাড়া চাহনি অদ্ভুত মোহময়! সহসাই বেহাগ বাজায় চেতনায়! তার নৃত্যভঙ্গি ঝড় তোলে মথুরার আকাশে বাতাসে! সবাই বলাবলি করতে লাগলো এতো মানুষ নয় যেন নন্দন কাননের অপ্সরা! উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা সবাইকে হার মানায় এই মেয়ে! সেই শিশু চন্দ্রকলায় কিশোরী হয়। চৌহদ্দির মাথারা একত্রিত হয়। তাঁদের অভিমত- চন্দ্রানির মতো সুন্দর লাস্যময়ী বালিকা এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয়টি নেই। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে সে হয়ে ওঠে সর্বশ্রেষ্ঠা। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন এই কিশোরীই হবে পরবর্তী নগর বালিকা। এখানে বলে রাখা ভালো যে নগর বালিকা উপাধি পাবে সে কোনদিন বিয়ে করতে পারবে না। বয়স বাড়লে তিনিই হবেন নগরবঁধূ। তিনি হবেন রাজ্যের মধ্যমণি। সবার মনোরঞ্জন করবেন, আর তাঁর নৃত্যকলা, সংগীত ও অভিনয় নৈপুণ্য দিয়ে সবার মন জয় করবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে ভর্তি করা হলো নৃত্যকলা পাঠশালায়। সেখানে তাঁকে শেখানো হলো- ভরতনাট্যম, নাট্য-বেদ আর ধ্রুপদী নৃত্যকলা। সেসময় নৃত্যশিল্প ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের কাছে কৃষ্টির এক অসাধারণ নিদর্শন। নগর বালিকারা যাত্রা, নাট্য চর্চা, ঝুমুর গান, পাঁচালী গীতি ও গীতি-কবির দোহার সহ অনেক ক্ষেত্রে গুণাবলী প্রকাশের সুযোগ পেতো। গোধূলি বেলার অর্ধ-স্তিমিত সূর্যের আলোটুকু জানান দেয় ব্যস্তময় দিনের পরিসমাপ্তির। এবার বিশ্রাম নেয়ার পালা। আবছা আলোকিত আলোকের নিচে প্রশান্ত মন নিয়ে ঘরে ফেরে তাবৎ প্রাণীকুল। মানুষও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। কর্ম-ক্লান্ত মথুরা-বাসীরা তখন ব্যস্ত দিনের শেষে রওনা হন নান্দনিক প্রশান্তির খোঁজে। নর্তকীদের শৈল্পিক ভঙ্গি সবার জন্য ছিল চরম উপভোগ্য ও আনন্দের। প্রতিটি চৌহদ্দিতে একটি করে নাটমন্দির ছিল। সেই নাটমন্দিরে নৃত্যকলা দেবীর পূজা হতো। আর সেখানে নৃত্য পরিবেশন করতেন বাছাই করা নর্তকীরা। এমনই একজন সর্বজন প্রিয় নর্তকী ছিলেন বাসবদত্তা। বাসবদত্তার চোখের চাহনি তীরের সুতীক্ষ্ণ ডগার মতো পুরুষের হৃদয়ে মধুর ব্যথার সৃষ্টি করে। তাদের চেতনা শিহরিত হয়। হৃদয়ের আবেগ উৎসারিত হয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তাঁদের সারা দিনের কর্ম ক্লান্ত দেহ-মন এক অপার্থিব পূর্ণতায় ভরে ওঠে। দিনের পর দিন এভাবেই চলতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা স্নান সেরে পুজোয় বসেন তিনি। সুগন্ধি তেলের প্রদীপ, আগরদান, ধুপের ধোঁয়া, জল, তেল, নৈবদ্য দিয়ে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেন প্রভুর চরণে। পূজা শেষে তিনি তার পূজা-বস্ত্র পরিত্যাগ করে নর্তকীর পোশাক পরিধান করেন। তাঁদের বিনোদনের গুরু দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। এটাই ছিল তার নিত্যকর্ম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা আসরের প্রস্তুতি শেষে গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি মেলে চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান তিনি। কি কারণে যেন তার মনটা আজ অনেক উচাটন। শ্রাবণের ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, সাথে বকুল ফুলের মিষ্টি গন্ধে তিনি আবেশিত হন। অবচেতন মনে এই অদ্ভুত অনুভূতি তিনি কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই তার গবাক্ষের দৃষ্টিসীমায় অপূর্ব সুন্দর সৌমকান্তি গৌরবর্ণ এক যুবক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। হঠাৎ করেই বিস্ময়ে থমকে গেলেন বাসবদত্তা! এই পৃথিবীতেও এমন সুন্দর সুদর্শন পুরুষও আছে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। তার নাটমন্দিরে শুধুমাত্র বয়সের ভারে ন্যুজ, ক্লান্ত-শ্রান্ত মধ্য বয়সীদের দেখেই সে অভ্যস্ত। কে এই সৌম্য কান্তি যুবক গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গেরুয়া বসন, কপালে চন্দনের তিলক আর হাতে ভিক্ষার ঝুলি! বাসবদত্তার মন বলছে- বাসবি এই হল তোর সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, যাকে তুই সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছিস! তিনি শিহরিত হন। আকুল প্রাণে নিজের পরিচারিকাকে মনের কথা খুলে বলেন। পরিচারিকা বাসবদত্তার মনের অবস্থা বুঝতে দেরি করে না। তিনি দৌড়ে গিয়ে নবীন সন্ন্যাসীর পথ রোধ করে দাঁড়ান। -হে প্রভু অপরাধ নেবেন না আমার অন্নদা আপনার সন্দর্শনে মোহিত। আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। নবীন সন্যাসী বলেন- আমি জানি সব কিছুই। কিন্তু এখনো তাঁর সাথে সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় আসেনি। সময় হলে আমি নিজে থেকে এসেই ধরা দেব। বাসবদত্তা ও তার পরিচারিকা উভয়ই ভীষণ আশ্চর্য ও আহত হন। এ পৃথিবীর তাবৎ পুরুষ কূল যার নৈকট্য লাভের আশায় আকুল প্রতীক্ষা করে, তাঁর একটুখানি স্পর্শ সুখের আশায় সমস্ত ধন রত্ন বিসর্জন দিতে পারে সেই রমণীকে প্রত্যাখ্যান করলেন একজন নবীন সন্ন্যাসী! বাসবদত্তার কেন যেন মনে হলো নবীন সন্ন্যাসী হয়তো উপঢৌকনের অপারগতার কারণে তার কাছে আসতে চাচ্ছেন না! কারণ তাঁর কাছে যারাই আসেন তাঁরাতো স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা-জহরত সহ বহুমূল্য রত্ন উপহার নিয়ে আসেন। তিনি আবারো পরিচারিকাকে পাঠালেন নবীর সন্ন্যাসীর কাছে। পরিচারিকা সন্যাসীকে বললেন- আমার অন্নদার কোন মূল্যবান ধন রত্নের প্রয়োজন নেই। তাঁর অঢেল আছে। তিনি মনে প্রাণে আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছেন! আপনি তাঁর ভালোবাসার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা গ্রহণ করুন। সন্ন্যাসীর মুখে আবার সেই প্রশান্তির হাসি- আমি আবারও বলছি সময় এখনো আসেনি। যখন সময় আসবে তখন আমি নিজে থেকেই তাঁর কাছে আসবো আমি কথা দিলাম। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলুন। পরিচারিকা সন্ন্যাসীর অবয়বে দৈবভাব ও দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে শঙ্কিত হলেন। তার মাথা বিনয়ে অবনত হলো। মুখ ফুটে আর কোন কথাই বলতে পারলো না। যুবক ধীর পদক্ষেপে অন্তরীন হলেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর নাম উপগুক্ত। তৎকালীন চরম নিঠুর মৌর্য সম্রাট-অশোকের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন তিনি। তিনি সম্রাট অশোককে সমস্ত ঘৃণা, হিংসা, রক্তপাত, রাজ্য জয়ের ইচ্ছা সহ সমস্ত মোহ পরিত্যাগ করে মানব জীবনের সত্যিকারের অর্থ ও মানবতার জয় গান গাইতে শেখান। তাঁর অপার্থিব ও মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষায় সম্রাট অশোক সম্পূর্ণ বদলে গেলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিলেন ও গেরুয়া পোশাক পরিধান করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে শুরু করলেন। এদিকে বাসবদত্তা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে গৃহকোণে আশ্রয় নিলেন। তাঁর অনুগামী, অনুরাগী, স্তাবক, বিদূষক যারাই তার কাছে আসতেন তিনি সবাইকে ফিরিয়ে দিলেন। এভাবেই দিনে দিনে তিনি লাবণ্য হারিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেলেন। পরিচারিকা প্রাণান্ত চেষ্টাও তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি একটি উপায় খুঁজে বের করলেন। তাঁর মনস্থিরের জন্য তিনি তাঁকে একটি ভাস্কর্য কারু মেলায় নিয়ে গেলেন। কারু-মেলার ভাস্কর্য দেখে বাসবদত্তা অভিভূত হলেন। বিশেষ করে একটি নারী ভাস্কর্য তাকে মোহিত করে। এতোই মোহিত করে যে তিনি ভাস্করকে দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না। তাঁর অনুরোধ ভাস্করের কাছে নিয়ে গেলে তিনি ভাস্কর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তখন ভাস্কর, বাসবদত্তার রূপের ছটায় মুগ্ধ হয়ে তার একটি ভাস্কর্য নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বাসবদত্তাকে কোনোভাবেই রাজি করাতে না পেরে ভাস্কর বললেন- পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য! শুধুমাত্র সৃষ্টিই নিত্য ও চিরকালীন। আপনি চলে যাবেন কিন্তু আপনার ভাস্কর্যের মাঝে আপনি বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল। ভাস্করের শিল্পকর্ম অমর! মৃত্যুর পরেও ভাস্কর ও তার ভাস্কর্য বেঁচে থাকবে হাজার বছর। আনন্দ আবেগের চোখে জল এসে গেল বাসবদত্তার। ভাস্কর্যের অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। বিকেলের গবাক্ষের আলোয় খোলা চুলে, নগ্নদেহে তিনি নিজেকে মেলে দিলেন ভাস্করের সামনে। ভাস্কর তখন তিল তিল করে, অনেকদিন প্রচেষ্টার পরে বাসবদত্তার একটি নান্দনিক ভাস্কর্য তৈরি করতে সক্ষম হলেন। বাসবদত্তা নিজের ভাস্কর্য দেখে এতই বিমোহিত হলেন যে তার দুচোখ থেকে অঝোর ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভাস্কর তাঁকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি বাসবী। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না। বাসবদত্তা নিশ্চুপ হয়ে তাঁর বুকের সাথে লেগে রইলো। তাঁর চোখেও আনন্দাশ্রু। যতই সময় গড়ায় ভাস্কর ও বাসবদত্তার ভালোলাগা আরো গাঢ় হয়। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা, ভালোবাসা থেকে প্রেম ও প্রেম থেকে পরিণয়ের দিকে যখন তারা ধাবমান তখন নিয়তি বাদ সাধলো। মথুরার লোক সমাজ একজন নগর-বঁধুর পাণিগ্রহণের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেননা। তাঁদের সিদ্ধান্ত: নগর-বঁধু একা কারো হতে পারেনা! সকলের অধিকার আছে নগর-বঁধুকে উপভোগ করার। এটাই পরম্পরা। তারা সর্বসম্মতিক্রমে ভাস্করকে হত্যা করলো। তাঁকে হত্যা করে বাসবদত্তার বাড়ির আঙিনায় পুঁতে রাখল। আর ষড়যন্ত্র করে ভাস্কর হত্যার অপরাধে বাসবদত্তাকে অভিযুক্ত করে তার নাটমন্দির, বাড়ি, আটচালা সব কিছু পুড়িয়ে দিল। পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে প্রাসাদের বাইরে দেয়ালের কিনারে ফেলে রাখলো। ক্রমে ক্ষত গাঢ় হতে লাগলো তার সৌন্দর্য রহিত হলো, শরীর শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেলো, পরিচারিকার আপ্রাণ চেষ্টা, সহানুভূতি ও চিকিৎসার কারণে শুধুমাত্র তার প্রাণটা অবশিষ্ট ছিল। একটি চর্মসার শরীর নিয়ে তিনি তখন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এই দুঃসহ সময়ে বাসবদত্তার সামনে এসে হাজির হলেন সেই সৌম্য-কান্তি নবীন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। মায়া ভরা চাহনিতে বললেন -বাসবদত্তা, তোমার ভালোবাসা আর অদম্য কাছে পাওয়ার ইচ্ছা আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছে। আমাকে তুমি তোমার সেবা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করোনা বাসবি। বাসবদত্তা অভিমানে বললেন -আপনি বলেছিলেন সময় হলে আসবেন এটা তো সময় নয়! এটা আমার চরম দুঃসময়! আমার শেষ নিঃশ্বাস দেখতে এসেছেন? বাসবদত্তা তাঁর কদর্য মুখ আঁচলে ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত রাখলেন। সান্ত্বনার সুরে বললেন - ন-হন্যতে হন্যমানে শরীরে। বিনয়ের সাথে সন্ন্যাসী অনুমতি চাইলেন তাঁকে মঠে নিয়ে সেবা করার জন্য। বাসবী নিজেকে সন্ন্যাসীর পায়ে সমর্পণ করলেন। ধীরে ধীরে সেবা যত্ন চিকিৎসা দিয়ে সন্যাসী তাঁকে সুস্থ করে তুললেন। আর তাঁর মানসিক ক্ষতকে সারিয়ে তোলার জন্য তিনি তাকে ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দিলেন। নিজের ভেতরের আলোকে প্রজ্বলিত করার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। মথুরার মক্ষীরানি, সর্ব-মনোহারিনী বাসবদত্তা তখন সর্ব-সুন্দরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি”  ড. রতন কুন্ডু, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া |
 Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025
Bangladesh Australia Disaster Relief Committee AGM 2025