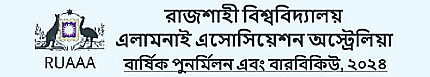এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিন
এই লিংক থেকে SolaimanLipi ডাউনলোড করে নিনমোনায়েম সরকার  সু-সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয় নি কো নজরুল।’ প্রথিতযশা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি শুধু নজরুল নন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভাগ হননি। বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের কাছে, সর্বোপরি বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তা। রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতিকে দিয়েছে অমরত্ব, বাঙালি জাতিকে দিয়েছে অসামান্য মর্যাদা। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাঙালির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকবেন। বাঙালির হৃদয়ে তার আসন চিরস্থায়ী। সু-সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/ আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ ভাগ হয় নি কো নজরুল।’ প্রথিতযশা সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি শুধু নজরুল নন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভাগ হননি। বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের কাছে, সর্বোপরি বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তা। রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতিকে দিয়েছে অমরত্ব, বাঙালি জাতিকে দিয়েছে অসামান্য মর্যাদা। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি পৃথিবীর বুকে টিকে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধার সঙ্গে বাঙালির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকবেন। বাঙালির হৃদয়ে তার আসন চিরস্থায়ী।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রতিভা। তিনি সাহিত্যের সব শাখাতে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করলেও তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় তিনি ‘কবি’। কবিতার জন্যই তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তার কবিতা শুধু বাঙালি পাঠককেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের কবিতা পাঠককেও আনন্দ দিচ্ছে অবিরাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, শান্তিতে-সংগ্রামে মানুষকে প্রেরণা দেয়। বাংলা ভূখণ্ডের বাইরে তথা পৃথিবীর দেশে দেশে আজো তার অগণিত কবিতা-পাঠক রয়েছেন। রবীন্দ্র কবিতার সুধা যিনি একবার পান করেছেন তিনিই রবি-প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। শুধু কবিতা নয়, রবীন্দ্রনাথের গানও বাঙালির চির আনন্দের ধন। রবীন্দ্রনাথের গান দোলা দেয় না- এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া ভার, প্রতি রাতে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে আমি নিদ্রামগ্ন হই। প্রভাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতেই ঘুম ভাঙে আমার। শুধু আমি নই, আমার মতো এ রকম কোটি কোটি ভক্ত আছেন রবীন্দ্র সঙ্গীতের। নানা বয়সের মানুষের জন্য সাহিত্যরস যুগিয়েছেন বাঙালি সন্তান রবি। মানব-মানবীর হৃদয়ের আবেগকে রবীন্দ্রনাথের মতো আর কোনো কবি শব্দে-ছন্দে-গানে রূপায়িত করেছেন বলে সাহিত্যের ইতিহাসে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন অখণ্ড বাংলায়। যদিও ভৌগোলিকভাবে বর্তমান ভারতবর্ষই তার জন্মভূমি ও সমাধি ক্ষেত্র, কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে তার নাড়ির যোগ। তার পূর্ব পুরুষেরা বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। বৈবাহিক সূত্রেও তিনি আবদ্ধ ছিলেন বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে। প্রায় এক যুগ তিনি বাংলাদেশেই নিজেদের জমিদারী তদারক করেছেন। তাই বাংলা ভাষা ও বাংলা ভূমি রবীন্দ্রনাথের মননে সব সময়ই অপরূপ আবেগে জাগরূক ছিল। তার রচিত শিল্প সাহিত্যে এসবের দৃষ্টান্ত সু-প্রচুর। আমি রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখিনি তবে নজরুলকে দেখেছি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকের মতো আমিও কলকাতায় ছিলাম রণাঙ্গনের সৈনিক ও সংগঠক হিসেবে। তখন কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তাঁর বাসভবনে যাই এবং প্রথম কবিকে স্বচক্ষে দেখি। জন্মদিন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র ঘর ফুলে ফুলে আবৃত। নজরুল নিবিষ্ট মনে কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছেন। পাশে বসে বিখ্যাত নজরুল-সঙ্গীত শিল্পী আঙ্গুরি বালা গান গাইছেন- ‘ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি’। কবির ঘর মানুষে, ফুলে এবং গানের সুরে মুখরিত। বাংলাদেশের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী লাখো বাঙালির পক্ষ থেকে কবিকে তাঁর জন্মদিনে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে সেদিন আমি নিজেকে ধন্য করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ না দেখলেও তার স্মৃতি বিজড়িত বেশ কয়েকটি জায়গা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি দেখেছি, লাল মাটি আর শাল বীথীতে ঘেরা শান্তি নিকেতন দেখেছি, দেখেছি শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসর ও ত্রিপুরার রবীন্দ্র-সদন। যখনই ওই সব জায়গায় গিয়েছি তখনই আমার মনে জেগে উঠেছে রবীন্দ্র স্মৃতি, অন্যরকম ভালো লাগা। আমাদের অনেকের মনেই কবি সম্পর্কে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। সেটি হলো রবীন্দ্রনাথ জমিদার পুত্র ছিলেন, সীমাহীন আরাম আয়েশ করেছেন, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন আর মনের সুখে কবিতা-গল্প, গান বা অন্যান্য সাহিত্য-শিল্প সৃজন করেছেন। কিন্তু যারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ন্যূনতম লেখাপড়া করেছেন- তারা জানেন জীবন-জীবিকার জন্য রবীন্দ্রনাথকেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো, তাকেও নানাভাবে অর্থোপার্জন করে পরিবার-পরিজন ও সামাজিকতা রক্ষা করে চলতে হতো। এ প্রসঙ্গে কবির স্নেহ-ধন্য মৈত্রেয়ী দেবীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- বাংলাদেশের খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরের বড় কাছাকাছি এসেছিলেন কবি। পদ্মার জলে ভাসছে তার নৌকা, তিনি দেখছেন দু’পাশের জীবনলীলা- কখনো বা কল্পনায় একেবারে তাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করছেন। “... কী আশ্চর্য সহৃদয় দৃষ্টিপাতে কবি দেখেছেন সুখ-দুঃখমাখা, হাসি-কান্নাভরা মানুষের বড় ভালোবাসার জীবন। আর দেখেছেন নদী-খাল-বিল, তাল-নারিকেল কুঞ্জ, অবারিত প্রান্তরে সূর্যোদয়ের ও অস্তের সমারোহ, মাথার উপরে স্তব্ধ নীলাকাশের জ্যোতির্বিকীর্ণ মহোৎসব- মানুষ ও প্রকৃতি দুই মিলেছে এক আনন্দ সঙ্গমে, সেই আনন্দে মগ্নচৈতন্য কবির জীবনভোগ- ইয়োরোপীয় কবি ও শিল্পীদের চেয়ে কত পৃথক। অধিকাংশ সময়েই সম্পূর্ণ একাকী কোনরকম পার্থিব ভোগবিলাস-শূন্য, দু’একখানি বই মাত্র সঙ্গী। গ্রামের ঘাটে বাঁধা বোটে মাঠের ধারে ক্ষেত্রের পাশে জোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে চলেছে কবির জীবন ভোগের রসোৎসব। (কুটির-বাসী রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)।” কলকাতার ঠাকুর বাড়ির জমিদার-পুত্র রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গে এসে কিভাবে দিনের পর দিন সঙ্গী সাথী-হীন জীবনযাপন করেছেন এসবের বিবরণ কবির লেখা বিভিন্ন চিঠিপত্রেও কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ‘ছিন্নপত্রে’ এসবের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কলকাতার রবীন্দ্রনাথ আর পূর্ব বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই এক রবীন্দ্রনাথ নয়। কলকাতায় থাকতে রবীন্দ্রনাথ দেখেছে নাগরিক জীবনের কোলাহল। তখন তার লেখার মধ্যে থাকতো নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গ। যেন কৃত্রিম আবেগে রচিত বুদ্ধিমান কবির রচনা। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এসে রবীন্দ্রনাথ যখন পা রাখলেন তখন তার লেখার বিষয় আপনা-আপনি বদলে যায়। তিনি যা দেখেছেন তা-ই তাঁর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতা বলি, গান বলি আর গল্প-ই বলি- পূর্ববঙ্গে বসে বসে কবি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা-ই মহৎ শিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আমরা শিলাইদহের কথা বলতেই পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার আনাচে-কানাচে জমিদারী তদারক করার জন্য অবিরাম ঘোরা-ফেরা করেছেন। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন অভিনব সব সাহিত্য প্রকরণ। এমন কি যে গীতাঞ্জলী কাব্য লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছিলেন সেই গীতাঞ্জলী কাব্যেরও বেশকিছু কবিতা লেখা হয়েছে শিলাইদহে বসে। তার মানে আমরা বলতেই পারি শুধু ভারতের মাটিই রবীন্দ্র জীবনে রসসঞ্চার করেনি, বাংলার মাটির রসও লেগে আছে রবীন্দ্র প্রতিভায়। বাংলার প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে অসীম প্রেরণা আর রবীন্দ্রনাথও সেই প্রেরণায় প্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেছেন তার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য-সম্পদ। এখানে আরেকটি কথাও বলে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ‘রবি বাউল’ বলে যে পরিচয় দিয়েছেন তার বাউল প্রীতির উৎস কিন্তু বাংলার শিলাইদহই। শিলাইদহে এসেই তিনিই পরিচিত হন লালন, গগন হরকরা, হাসন রাজার মতো বাউল কবিদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলের সুর যুক্ত হওয়ার পেছনেও আছে শিলাইদহে বসবাসের প্রেরণা। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথ যে সুর সংযোগ করেছেন সেই সুরটিও তিনি নিয়েছেন গগন হরকরার- আমি কোথায় পাবো তারে আমার মনের মানুষ যে রে’ এই গানের সুর থেকে। শিলাইদহ, শাহজাদপুর, পতিসরের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের চৈতন্যে মৃত্যু অবধি ক্রিয়াশীল ছিল। বাংলা প্রীতি ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি চিরদিনই দায়বদ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার সেই দায়বদ্ধতার কথা আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি বা পেরেও না বোঝার ভান করেছি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে ছিলেন। কেন ছিলেন? তিনি কি মনে মনে কামনা করেছিলেন অখণ্ড বাংলা? আজ বিশ্বের দেশে দেশে দেখছি ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের বিশেষ দুর্বলতা, সবাই এখন ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রের দিকেই বেশি করে ঝুঁকছে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নেও কি ছিল অখণ্ড বাংলা ভূমি? সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার শান্তি নিকেতনে নিজস্ব অর্থায়নে ভবন নির্মাণ করে শান্তি নিকেতনের শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়েছেন। বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে এদেশের মানুষকে আরো বেশি রবীন্দ্র চেতনার সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ এনে দিয়েছেন। এগুলো সবই আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অসমাপ্ত কাব্য ‘শেষ লেখা’র এগারো সংখ্যক কবিতায় বলেছিলেন- “রূপনারানের কূলে / জেগে উঠিলাম, / জানিলাম এ জগৎ / স্বপ্ন নয়।/রক্তের অক্ষরে দেখিলাম।/আপনার রূপ,/চিনিলাম আপনারে/ আঘাতে আঘাতে/ বেদনায় বেদনায়;/ সত্য যে কঠিন,/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,/ সে কখনো করে না বঞ্চনা।” সত্য আসলেই কঠিন এবং অখল। সত্য কখনোই বঞ্চনা করে না। এর প্রমাণ দু’শ বছর পরে নিজ দেশ জার্মানিতে কার্ল মার্কসের ভাস্কর্য স্থাপনে দেখতে পাই। বাংলা-প্রেমী রবীন্দ্রনাথকেও একদিন বাংলা-বিদ্বেষী পাকিস্তানিরা বর্জন করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ আজ বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হয়ে উঠেছেন। বহুধারায় বিভক্ত বাঙালি জাতিকে রবীন্দ্রনাথই পারেন ঐক্যবদ্ধ করতে, এমনকি টুকরো টুকরো বাংলা ভূখণ্ড ও আবার জোড়া লাগাতে সাহায্য করতে পারে রবীন্দ্র-চেতনা। বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি রবীন্দ্র-নির্ভর হলে আমাদের উত্থান অবধারিত। এই কথাটি আজ আমাদের ভাবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বাংলা ও বাঙালির অহংকার রবীন্দ্রনাথকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। মোনায়েম সরকার: রাজনীতিবিদ ও কলামিস্ট - ০৭ মে, ২০১৮ |