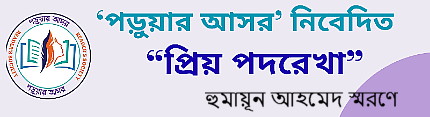ড. নজরুল ইসলাম  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা চলে গেলাম ভার্না। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত ভার্না বুলগেরিয়ার বৃহত্তম বন্দর এবং তৃতীয় বৃহত্তম শহর। সোফিয়ার তুলনায় ভার্না বেশ ছোট শহর। ভার্নার জনসংখ্যা সোফিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ। রাজধানী সোফিয়ায় বছর খানেক বসবাস করার পর দুই শহরের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ছিলো। এখানে উঁচু ভবন নেই বললেই চলে। এখানকার সরকারি এবং আবাসিক ভবনগুলোর নকশায়ও কিছুটা ভিন্ন ধরণের। সবকিছুই কাছাকাছি। এখানে ট্রাম নেই। বাস ভাড়াও সোফিয়ার তুলনায় কম। সারা শহর জুড়ে রয়েছে রোমান শাসনের অসংখ্য নিদর্শন। যার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত বাথ কমপ্লেক্স (রোমান থার্মে), ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম সংরক্ষিত রোমান থার্মে এবং বলকান অঞ্চলে বৃহত্তম। ভার্নার প্রধান আকর্ষণ হলো এর সমুদ্র সৈকত, যা বিশ্বের সেরাগুলোর মধ্যে অন্যতম। শহরের উপকূলে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর পার্ক, বুলগেরিয়ান ভাষায় যার নাম 'মরস্কা গ্রাদিনা' (সি গার্ডেন)। পরবর্তীতে এই পার্কটি আমাদের সময় কাটানোর প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। সময় পেলেই হাসুকে নিয়ে ঘুরতে চলে যেতাম এই পার্কে। দীর্ঘ ছুটি কাটানোর পর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা চলে গেলাম ভার্না। কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে অবস্থিত ভার্না বুলগেরিয়ার বৃহত্তম বন্দর এবং তৃতীয় বৃহত্তম শহর। সোফিয়ার তুলনায় ভার্না বেশ ছোট শহর। ভার্নার জনসংখ্যা সোফিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ। রাজধানী সোফিয়ায় বছর খানেক বসবাস করার পর দুই শহরের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ছিলো। এখানে উঁচু ভবন নেই বললেই চলে। এখানকার সরকারি এবং আবাসিক ভবনগুলোর নকশায়ও কিছুটা ভিন্ন ধরণের। সবকিছুই কাছাকাছি। এখানে ট্রাম নেই। বাস ভাড়াও সোফিয়ার তুলনায় কম। সারা শহর জুড়ে রয়েছে রোমান শাসনের অসংখ্য নিদর্শন। যার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত বাথ কমপ্লেক্স (রোমান থার্মে), ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম সংরক্ষিত রোমান থার্মে এবং বলকান অঞ্চলে বৃহত্তম। ভার্নার প্রধান আকর্ষণ হলো এর সমুদ্র সৈকত, যা বিশ্বের সেরাগুলোর মধ্যে অন্যতম। শহরের উপকূলে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর পার্ক, বুলগেরিয়ান ভাষায় যার নাম 'মরস্কা গ্রাদিনা' (সি গার্ডেন)। পরবর্তীতে এই পার্কটি আমাদের সময় কাটানোর প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। সময় পেলেই হাসুকে নিয়ে ঘুরতে চলে যেতাম এই পার্কে।আমাদের থাকার জায়গা হলো এখানকার ছাত্রাবাসে। পাশাপাশি তিনটি ব্লক নিয়ে এই 'স্টুডেন্টস কমপ্লেক্স'। সেই সময়, ভার্না শহরে তিনটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল: ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য, হায়ার ইন্সটিটিউট অফ মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্না, মেডিসিনের জন্য, মেডিকেল একাডেমী ভার্না এবং অর্থনীতির জন্য, হায়ার ইন্সটিটিউট অফ ইকোনমিক্স ভার্না। বর্তমানে এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল আলাদা আলাদা ব্লক। এখানে প্রতিটি রুমে তিনজন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা ছিল, যেখানে সোফিয়াতে ছিল চারজন। আমরা তিন বাংলাদেশি – আনোয়ার (বর্তমানে স্টোকহোম-বাসি), কামরুল (বর্তমানে ডালাস-বাসি) ও আমি – রুমমেট হয়ে গেলাম। হোস্টেলের কাছেই ছিল ডাইনিং হল এবং একটা ছোট ক্যাফেটেরিয়া। মেডিকেল একাডেমী, হোস্টেল থেকে ১০ মিনিটের পথ। মেডিকেল একাডেমীর সঙ্গেই লাগানো ছিল ইকোনমিক্স ইন্সটিটিউট। ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট ছিল একটু দূরে; বাসে যাতায়াত করতে হতো। ভার্নায় থিতু হওয়ার পর একদিন আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে চলে গেলাম ভর্তি হওয়ার জন্য। সঙ্গে নিলাম বুলগেরিয়ান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠি, ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স সম্পন্ন করার সার্টিফিকেট এবং দুই কপি ছবি। আমরা সরকারি বৃত্তি নিয়ে পড়তে এসেছি 'শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং', আমাদের অফার লেটারে তাই লেখা ছিল। এখানে এসে জানতে পারলাম শিপবিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির নাম। এই ফ্যাকাল্টিতে দুটি বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে: নেভাল আর্কিটেকচার এবং মেরিন পাওয়ার মেশিনস অ্যান্ড মেকানিজমস। দুটি বিষয়ের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করার পর আমাদের ‘মেরিন পাওয়ার মেশিনস অ্যান্ড মেকানিজমস’ বিষয়টা পছন্দ হলো। আমরা চারজন (তিন রুমমেট এবং মোস্তফা) এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা হলো একটা সম্মিলিত ব্যাচেলর এবং মাস্টার কোর্স যা ৫ বছরে শেষ করতে হবে। পাঁচতলা ভবনের দোতালায় ফ্যাকাল্টি অফিস। আমাদের কাগজপত্র যাচাই করার পর সেক্রেটারি আমাদের ভর্তি করে নিলেন। সেই সঙ্গে সবাইকে দিয়ে দিলেন একটি করে লাল রঙের ‘লগবুক’। বুলগেরিয়ান উনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত প্রতিটি শিক্ষার্থীর একটা লগবুক থাকে যাতে শিক্ষার্থীর সমস্ত একাডেমিক কার্যকলাপের বিবরণ নথিভুক্ত করা হয়। লগবুকটা শিক্ষার্থীর কাছেই থাকে। এতে অনেক ছোটোখাটো বিষয়ও লিপিবদ্ধ থাকে, যেমন অসুস্থতার কারণে ক্লাসে অনুপস্থিতির জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট। ভর্তি হওয়ার পর ক্যাম্পাসটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সুন্দর খোলামেলা ক্যাম্পাস। খেলাধুলা এবং বিনোদনের জন্য রয়েছে ইনডোর এবং আউটডোর স্টেডিয়াম। ভবনগুলো তুলনামূলক ভাবে নতুন, তাদের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের পর। মেইন বিল্ডিংয়ের নিচতলায় ছিল ওভারকোট রাখার জন্য একটা বিশাল 'ক্লোকরুম', তার পাশেই ছিল একটা বড় ক্যান্টিন। আর ধূমপায়ীদের জন্য ছিল একটা নির্ধারিত এলাকা। মেইন বিল্ডিংয়ের কাছেই ছিল ডাইনিং হল। দোতালা ডাইনিং হলে ছিল শ’খানেক শিক্ষার্থীর খাবার ব্যবস্থা। আমরা ডাইনিং হলে দুপুরের খাবার সেরে হোস্টেলে ফিরলাম। ১৯৭৩ সালের ১৫ অক্টোবর সোমবার ছিল আমাদের ইউনিভার্সিটি জীবনের প্রথম দিন। সেই দিনটার কথা আজ মনে পড়ে। আমরা চার বাংলাদেশী সহপাঠী সকাল সকাল ইউনিভার্সিটি পৌঁছে গেলাম। আমাদের প্রথম ক্লাস ছিল ‘লিনিয়ার অ্যালজেবরা’, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া চারটি গণিত বিষয়ের মধ্যে একটি। ক্লাসে বসে আছি আমরা জনা তিরিশেক ছাত্র-ছাত্রী। সেটা ছিল একটা টিউটোরিয়াল ক্লাস। ক্লাস নিচ্ছিলেন একজন তরুণ মহিলা শিক্ষক, সম্ভবত একজন গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। এই বিষয়ে লেকচার তখনো শুরু হয়নি, তাই চলছিল আগের জ্ঞানের রিভিশন। প্রথমে ম্যাডাম সেদিনের পাঠের তাত্ত্বিক অংশের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে আমাদের সমাধান করতে বললেন। সবাই মনোযোগ দিয়ে খাতায় সমাধান লিখছে আর ম্যাডাম ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কাজ দেখছেন। তিনি আমার কাছে পৌঁছানোর আগেই আমি অঙ্কটার সমাধান করে ফেলেছি। আমার কাজ দেখে ম্যাডাম জানালেন উত্তর সঠিক হয়েছে এবং আমাকে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটার সমাধান করতে বললেন। আমি বোর্ডে অঙ্কটার সমাধান লিখলাম এবং ভাষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যতটা পারি সহপাঠীদের বুঝিয়ে বললাম। পরবর্তীতে অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল – সেদিন বাংলাদেশি ছাত্ররাই বোর্ডে সব অংকের সমাধান করেছিল। গণিতে বাংলাদেশী ছাত্রদের দক্ষতা দেখে সবাই অবাক! প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনিভার্সিটিতে যোগদান করার আগে বুলগেরিয়ান ছাত্রদের দুই বছর ব্যাপী বাধ্যতামূলক আর্মি ট্রেনিং নিতে হয়। এই দুই বছরে পড়াশুনার অনেক কিছুই তারা ভুলে গেছে। প্রথম সেমিস্টারে আমাদের বিষয় ছিল পাঁচটি: গণিত (দুটি বিষয়),পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং বুলগেরিয়ান কমুনিস্ট পার্টির ইতিহাস। সব মিলিয়ে প্রতি সপ্তাহে ছিল ১২ ঘণ্টা লেকচার এবং ১০ ঘণ্টা টিউটোরিয়াল ক্লাস। ক্লাস হতো সপ্তাহে ছ’দিন। সেই হিসাবে, প্রতিদিন গড়ে ক্লাস ছিল ৩.৭ ঘণ্টা। অর্থাৎ ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দেয়ার প্রচুর সময়। ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্সটিটিউটে সারাদিন ধরে ক্লাস চলতো; তাই আড্ডা দেয়ার কোনো সুযোগ ছিলোনা। ধীরে ধীরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ইতিমধ্যে কিছু বুলগেরিয়ান বন্ধু জুটেছে। বুলগেরিয়ায় পড়াশুনা ছিল সম্পূর্ণ লেকচার/টিউটোরিয়াল নির্ভর। অর্থাৎ ক্লাসে যা পোড়ানো হতো সেটুকু জানলেই হলো। লাইব্রেরিতে বসে রেফারেন্স বই দেখার বালাই ছিল না। টিউটোরিয়ালে রোল কল নেয়া হতো, তাই ফাঁকি দেয়া যেত না। লেকচার অনুষ্ঠিত হতো প্রায় দুশো ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে একটা বড় লেকচার হলে। মাঝে মাঝে লেকচার ফাঁকি দিতাম। কার্বন পেপার আর কাগজ দিয়ে রাখতাম বুলগেরিয়ান বন্ধুদের কাছে যাতে লেকচারের কপি পেয়ে যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন কালে, মেয়েরা আমার এই গল্প শুনে অবাক হতো, আমরা ফটোকপি ছাড়া কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলাম। এখন অবশ্য এখন ফটোকপির যুগেও শেষ। এখন লেকচারের কপি এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। দুপুরের পর ক্লাস না থাকলে মাঝে মাঝে আমরা চার বাংলাদেশী সহপাঠী চলে যেতাম সিটি সেন্টারে। প্রধান সড়ক ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম। মোস্তফা ছিল আমুদে প্রকৃতির লোক, কিছুটা বেহিসাবি। বলা নেই কওয়া নেই, পকেটে টাকা নেই, সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়তো রেস্তোরাঁয়। আর বিল পরিশোধ করতে হতো আমাদের। প্রসঙ্গত, মোস্তফা ছিল চেইনস্মোকার, তাই কখনই ওর আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। ইতিমধ্যে হাসুর সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক দিন দিন গাড়ো হচ্ছে। দুজনেই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত; আমার চেয়ে হাসুর পড়ালেখার চাপ ছিল বেশি। কেননা সে ছিল মেডিসিনের ছাত্রী। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা দেখা করতাম এবং একসাথে কিছু সময় কাটাতাম। সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল রোববার। সেদিন আমরা সারাদিন একসাথে কাটাতাম – যার মধ্যে ছিল পার্কে ঘুরে বেড়ানো, সিনেমা দেখা এবং রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করা। কখনো কখনো বাংলাদেশী সহপাঠীদের সাথে নিয়ে যেতাম। বিশেষ করা যখন যেতাম ভার্নার বাইরে ডে ট্রিপে। সবাই একসঙ্গে মজা করে দিনটা কাটাতাম। আমাদের সেমিস্টার ছিল ১৫ সপ্তাহব্যাপী। ব্যস্ততার মাঝে ১৫ সপ্তাহ কেটে গেলো। এই ব্যস্ততার কারণ, আমাদের প্রতি সপ্তাহে থাকতো কুইজ, ক্লাস টেস্ট এবং এসাইনমেন্ট। বুলগেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'কন্টিনিউয়াস এসেসমেন্টের' উপর জোর দেয়া হয়েছিল। কন্টিনিউয়াস এসেসমেন্টে সবসময় ভালো করার চেষ্টা করতাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা নিয়ম চালু ছিল – যদি কারো কন্টিনিউয়াস এসেসমেন্টের মার্ক ‘ক্রেডিট’ বা তার বেশি থাকে সে ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া ছাড়াই কন্টিনিউয়াস এসেসমেন্টের ভিত্তিতে ফাইনাল গ্রেড পেতে পারে। এই নিয়মের বদৌলতে, ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া ছাড়াই দুটি গণিত বিষয়ে হাই ডিস্টিংশন পেয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুটি পরীক্ষায় হাই ডিস্টিংশন পাওয়া খুবই খুশির খবর। তাছাড়া এতে করে বাকি তিনটি বিষয়ের প্রস্তুতির জন্য বেশি সময় পেয়ে গেলাম। বুলগেরিয়ান পরীক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য দেশের তুলনায় ভিন্ন। প্রথমত, এখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে হয়। শিক্ষকরা পুরো সিলেবাস থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের কম্বিনেশন নির্বাচন করে খামে ভোরে রাখেন। পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার পর, শিক্ষার্থীকে একটা খাম তুলে নিতে হয় এবং তাকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয়। ফলে সম্পূর্ণ সিলেবাস আয়ত্ত না করলে পাশ করা কঠিন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সবার প্রশ্নপত্র একই থাকে, তাই প্রশ্নপত্র কিছুটা অনুমান করা যায়। যেমন, এই প্রশ্নটা গত বছরের পরীক্ষায় এসেছিল তাই এই বছর এটার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাজেই সম্পূর্ণ সিলেবাস আয়ত্ত না করলেও চলে। যদিও এতে কিছুটা ঝুঁকি থাকে, তবে ঝুঁকির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম। দ্বিতীয়ত, এখানকার পরীক্ষা পদ্ধতি লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষার সংমিশ্রণ। খাম তুলে নেয়ার পর উত্তর প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার্থীকে ঘণ্টা-খানেক সময় দেয়া হয়। এরপর শিক্ষার্থীকে পরীক্ষকের সামনে বসে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উত্তর মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। ভাষার ঘাটতির কারণে আমরা লিখিত উত্তর প্রস্তুত করতাম। লিখিত উত্তর দেখার পর পরীক্ষক অতিরিক্ত প্রশ্ন করতেন। অর্থাৎ সঠিক উত্তর লেখাই যথেষ্ট নয়; বিষয়টা সামগ্রিকভাবে জানতে হবে। আর উত্তর ভুল হোল তো কথাই নেই, শিক্ষার্থীকে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। আমার বিশ্বাস, এই পরীক্ষা পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করার সর্বোত্তম উপায়। বুলগেরিয়ান পরীক্ষা পদ্ধতির আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরীক্ষার ফল পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই পাওয়া যায়। প্রাপ্ত গ্রেড পরীক্ষক শিক্ষার্থীর লগবুকে লিখে দেন। বুলগেরিয়ায় ছয় পয়েন্টের গ্রেডিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, যেখানে ৬ হলো সর্বোচ্চ এবং ২ হলো সর্বনিম্ন গ্রেড: ৬ হলো এক্সসেলেন্ট (অস্ট্রেলিয়ায় যাকে হাই ডিস্টিংশন বলা হয়), ৫ ভেরি গুড (ডিস্টিংশন), ৪ গুড (ক্রেডিট), ৩ স্যাটিসফ্যাক্টরি (পাশ) এবং ২ পুওর (ফেল)। বুলগেরিয়ান শিক্ষার্থীদের মাঝে একটা জোক প্রচলিত ছিল – ৩ এবং ২ এর মধ্যে ব্যবধান হলো এক বছর। অর্থাৎ ২ পেলে শিক্ষার্থীকে সেই বছর পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অবশ্য ফেল করলে প্রতি সেমিস্টারে দুটি বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ ছিল। এইভাবে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমরা ডিগ্রী অর্জন করছি। এই কারণে, আমরা যারা বুলগেরিয়া এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে ডিগ্রি অর্জন করছি, তাদের প্রতিটি বিষয়ে শক্তিশালী মৌলিক জ্ঞান রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা যখন বাংলাদেশে ফিরে যাই, তখন আমাদের ডিগ্রিগুলো যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। অবশ্য এর প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক; যে সরকার আমাদের বিদেশ পাঠিয়ে ছিল, ততদিনে সেই সরকারের পতন ঘটেছে। আমি দীর্ঘ দিন অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেছি। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, আমাদের ডিগ্রি পশ্চিমা দেশের ডিগ্রীর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা যারা সমাজতান্ত্রিক দেশে পড়তে গিয়েছিল তারা ছিল বাংলাদেশের সেরা ছাত্র; অনেকেই এসএসসি/এইচএসসি-তে স্ট্যান্ড করা। তারা দেশে বসে থাকার পাত্র নয়। জীবিকার সন্ধানে অনেকেই বাংলাদেশে ছেড়ে চলে যায়। আমাদের ব্যাচের ১০ জনের মধ্যে মাত্র দুজন বাংলাদেশে স্থায়ী হয়েছিল। বাকি ৮ জনের মধ্যে চারজন অস্ট্রেলিয়ায়, দুজন সুইডেনে, একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বেছে নিয়েছে। তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজ নিজ পেশায় সাফল্য অর্জন করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। (চলবে)  সহপাঠী আনোয়ারের সাথে হাসু আর আমি  আগের পর্ব আগের পর্ব         পরের পর্ব পরের পর্ব   ড. নজরুল ইসলাম, কার্টিন ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া |